
パパ活でお付き合いをしている男性を好きになったらどうしたら良いのか悩んでいませんか。
好きになったとしても問題ないならパパ活を始めたいと思っている人もいるでしょう。
この記事ではパパを好きになったときの考え方を解説します。
本気でお付き合いしても大丈夫なのか、注意すべき点は何なのかを詳しく理解してパパ活をしていきましょう。
好きになってしまうのは悪くありません

結論としてはパパ活で男性を本気で好きになったとしても、何も悪いことはありません。
パパを好きになったのは良い人に恵まれたからです。
ずっと同じ男性とパパ活をしていても、あくまでお手当をもらうための関係で、好きという気持ちが出てこないこともあります。
お金のために割り切っていて、ちょっとくらい嫌なお付き合いだったとしても我慢していることがパパ活では多いからです。
本気で好きになってしまうくらいのパパに出会えたのはむしろ幸運でしょう。
最初はお手当目的だったとしても、数回のパパ活を通して恋心が芽生えてきてしまう人は決して少なくありません。
好きになるほどの魅力的なパパに出会えたのは運が良かったと前向きに捉えましょう。
自分の感情を押し殺そうとすると、パパとの関係に支障をきたすかもしれません。
パパとしてもうわべではなく、本気で好きになってくれると喜びます。
自分の感情を素直に受け入れて、これからどんなお付き合いをしていくかを、パパと相談してみるのがおすすめです。
パパと本気のお付き合いをするメリット
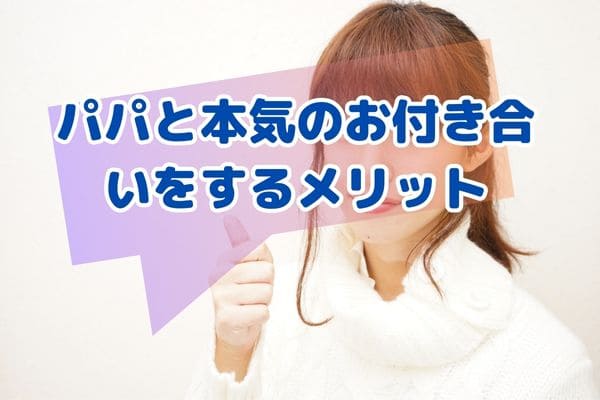
パパ活では本気で好きになってお付き合いをするとメリットがあります。
好きになったとしてもネガティブに考える必要はない理由をよく理解しておきましょう。
安定した経済的サポートが受けられる
パパを好きになったら安定してお小遣いをもらえるようになるのがメリットです。
経済的サポートを求めてパパ活を始めようと思った人が多いでしょう。
パパが一緒にいたいと思ってくれるようになれば、ずっとお付き合いを続けていくことができます。
好きになって本気でお付き合いをするとパパの満足度も飛躍的に向上します。
突然、パパ活をやめることになりにくいだけでなく、お手当も上げてくれる可能性が高くなるでしょう。
関係がより深まり心身健康に
好きになったらお互いの距離が近くなります。
関係が今までよりもずっと深まっていくでしょう。
お付き合いしたいという気持ちで毎回会ってデートをしているのでストレスもあまりありません。
お小遣いのために無理をすることもないでしょう。
パパ活を通して自分自身が元気になり、日々が充実することもよくあります。
心身ともに健康になれるパパ活ができるのは、パパを好きになった人だけのメリットです。
お互いヒミツが無くなり知識や人脈が拡大
パパにも好きになってもらえたら、普通の彼氏・彼女の関係になれます。
パパ活の関係の場合には、周囲に知られないようにしたいという気持ちが強いのが普通です。
お互いのことを深く知らないまま、うわべだけのお付き合いをすることになりがちです。
しかし、パパとお互いに好きという関係になれたら、もはやお互いにヒミツの関係を通そうとする意味がなくなります。
お互いの本名なども知ることができ、それぞれの友人を紹介し合ってコミュニケーションを取れるようになるのがメリットです。
パパと本気でお付き合いをするときの注意点

パパを好きになった場合にはトラブルになるリスクもあるのは確かです。
ここではパパ活で本気のお付き合いをしたいと思ったときに押さえておくべき注意点を紹介します。
パパが既婚者だった場合は不倫となりリスクが大きい
パパ活で相手を好きになったときに、既婚者だった場合には不倫のリスクがあります。
もし大人の関係をしたことがパパの配偶者にバレてしまったら、損害賠償や慰謝料を請求される可能性があるので気を付けましょう。
大人の関係でパパ活をするときには法律的に不倫と見なされることになります。
パパが本気になって離婚して交際したいという話になる場合もあります。
離婚調停がうまくいかずに周囲の人も巻き込んで大きなトラブルになることもあるため、既婚者のパパとは不倫関係にならないように細心の注意を払うことが必要です。
周囲の理解と社会的な偏見
パパ活で男性を好きになったときに周囲の理解を得られないリスクがあります。
年齢差が大きかったり、出会いのきっかけがパパ活だったりすると偏見を持たれることもあるので注意が必要です。
パパ活で出会ったことを内緒にしていても、あまりにも年齢やステータスに違いがあって不審に思われてしまう場合もあります。
お互いに社会生活が難しくなってしまうリスクがあるため、本気で好きになって大丈夫かどうかは慎重に吟味しましょう。
パパの束縛や制約の可能性
パパを一方的に好きになったときには、パパから束縛や制約を受ける場合があります。
パパと会える機会が減ったり、会うときにはもっと遠くでの待ち合わせになったり、街中デートができなくなったりするのが典型例です。
パパが周囲に知られたくないけれどパパ活は続けたいと思ったときによくあるパターンです。
束縛を受けたくないなら、好きという感情は押し殺してお付き合いした方が良い場合もあることは頭に入れておきましょう。
パパにとっては単なる遊び相手である可能性
パパを本気で好きになったとしても、パパは遊びの気持ちのこともあります。
パパが本気になってくれなかったら恋は成就しません。
本気になって良い相手かどうかは最初に見極めておくことが大切です。
うわべでは本気のように見せておきながら、自分の都合が悪くなった時点で彼女がいる、妻がいると言われてしまうこともあります。
パパを本気で好きなってしまった女性の体験談

ここではパパ活でパパを好きになった女性の経験談を紹介します。
実際に本気になった人がどうしているのかを知って、どうやって付き合っていくかを考えてみましょう。
お互いどちらかに「好き」の感情が芽生えたらお別れします
好きになったら終わりにすると最初の顔合わせのときに決めてパパ活を始めました。
私が本気になってしまいそうな気がしたので、お別れを告げて今に至っています。
年の差彼氏として交際をしています!
パパが本気で好きになってしまってどうしようか迷いました。
思い切って告白したらOKしてくれたので、今でも年の差彼氏として交際を続けています。
お互い本気と思っていたのに裏切られた
パパが好きになってアプローチしていたら、パパから好きだと言ってくれて本気のお付き合いを始めました。
なのに、この前、既婚だと言われてお付き合いが終わりになって悔しいです。
パパ活は裏切られる可能性があるので、決して本気になってはならないとよくわかりました。
まとめ

パパ活を通してパパを好きになったときの対策についてこの記事では以下のポイントを説明しました。
- パパ活でパパを好きになったとしても大丈夫なこと
- 本気でパパとお付き合いするメリットと注意点
- パパを好きになった人の体験談
パパをもし好きになったとしてもうまく関係を作り上げることは可能です。
リスクもあるので、本気になるときにはその後の関係がどうなるかをよく考えてから決めましょう。

